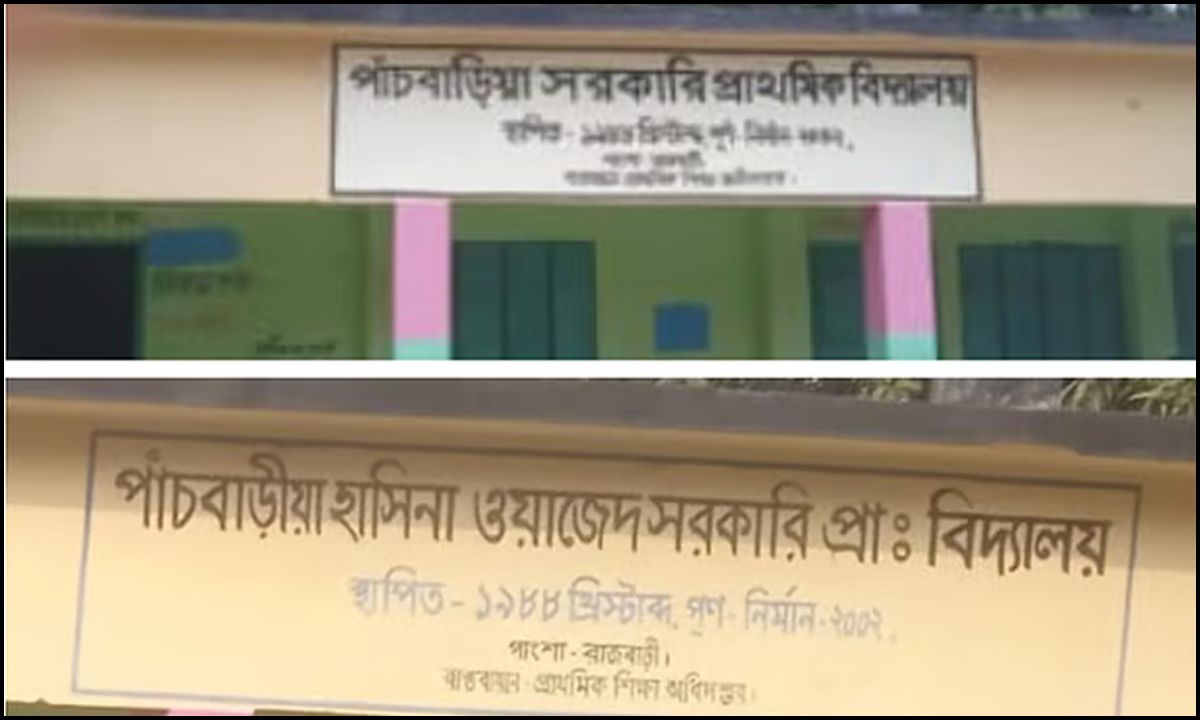গত বছরের তাপমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে চলতি বছরের রেকর্ড। পরপর কয়েক মাস তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর রেকর্ড করা হয়েছে।
২০২৪ সাল শেষ হওয়ার পথে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হওয়ার পথে রয়েছে। বর্তমানে আজারবাইজানের বাকুতে চলমান কপ ২৯ জলবায়ু সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রকাশিত সর্বশেষ ‘স্টেট অব দ্য ক্লাইমেট রিপোর্টে’ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এক ভয়ংকর চিত্র হাজির করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, তাপমাত্রা রেকর্ড শুরু হওয়ার পর ২০১৫-২০২৪ সবচেয়ে উষ্ণ দশক। বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা একটানা ১৬ মাস ধরে (জুন ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪) সম্ভবত আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রায়শই ব্যবধান বাড়ছে। এছাড়া চলতি বছর জানুয়ারি এবং সেপ্টেম্বরের গড় বৈশ্বিক বায়ুর তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প গড় থেকে এক দশমিক পাঁচ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। তাপমাত্রার এ উত্থানের অর্থ হলো বিগত মাসগুলোতে বিশ্ব প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। বার্কলে আর্থের জলবায়ু বিজ্ঞানী জেকে হাউসফাদার বলেছেন, ২০২৪ হলো সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। ২০২৩ ছিল গ্রহের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। বলা হয়, সম্ভবত গত এক লাখ বছরের মধ্য পৃথিবী সবচেয়ে উষ্ণতার রেকর্ড গড়েছে গত বছর। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস জানাচ্ছে, মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমন উষ্ণ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস
২০১৫ সালের কপ ২১ জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ সম্মত হয় প্যারিস চুক্তিতে। যার লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক উষ্ণতাকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ করা এবং দেড় ডিগ্রিতে আটকে রাখা। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করেছেন যে, এই নিম্ন প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করার অর্থ হলো পৃথিবীর একটি বিপদ অঞ্চলে প্রবেশ করা, যেখানে জলবায়ু আরও উষ্ণতা তৈরি করতে পারে। ইইউ-এর কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের চলতি মাসে প্রকাশিত একটি পৃথক প্রতিবেদনের উপসংহারেও বলা হয়েছে যে, এ বছরের জন্য বার্ষিক তাপমাত্রা সম্ভবত এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রির বেশি হবে। কোপার্নিকাস ডিরেক্টর কার্লো বুওনটেম্পো বলেছেন, প্রকৃতির এই উষ্ণায়ন আমার মনে হয়েছে উদ্বেগজনক। ওয়ার্ল্ড মেটারোলজিক্যাল অরগানাইজেশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আপাতত দেড় ডিগ্রি থ্রেশহোল্ড পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব মনে হচ্ছে না। যাকে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতা বলা যায়। দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রায় এক দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে না। ডব্লিউএমও সেক্রেটারি জেনারেল সেলেস্ট সাওলো বলেন, দৈনিক, এল নিনো এবং লা নিনার মতো প্রাকৃতিক ঘটনার কারণে মাসিক এবং বার্ষিক টাইম স্কেলে রেকর্ড করা বৈশ্বিক তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তনের প্রবণতা রয়েছে। ডব্লিউএমওর প্রতিবেদনে দেড় ডিগ্রি চিহ্ন অতিক্রম করার আগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জোর দেওয়া হয়। তারা সতর্ক করে যে, উষ্ণায়নের একটি ডিগ্রির প্রতিটি ভগ্নাংশ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে ন্যূনতম তাপমাত্রা বৃদ্ধি জলবায়ুর চরম অবস্থাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরা এবং দাবানলের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা ইতিমধ্যেই বিশ্ব জুড়ে বিপর্যয়কর ক্ষতির কারণ হচ্ছে।
গ্রিনহাউজ গ্যাস
ডব্লিউএমও জানাচ্ছে, ইতিমধ্যে ২০২৩ সালের রেকর্ডে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের সর্বোচ্চ মাত্রা দেখিয়েছে এবং রিয়েল টাইম ডাটা ইঙ্গিত দেয় যে তা ২০২৪ সালে বাড়তে থাকবে। ১৭৫০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তাপ পরিমাপে দেখা যায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা বিশ্বের মহাসাগরগুলোর উষ্ণতা পরিমাপ করে জানা যায়। এসব মহাসাগর বৈশ্বিক উষ্ণতার ৯০ শতাংশ তাপ শোষণ করে। মহাসাগরগুলো ২০২৩ সালে রেকর্ড তাপে পৌঁছেছে এবং ২০২৪-এর প্রাথমিক তথ্য দেখায় যে সেই প্রবণতার ধারাবাহিকতা বজায় আছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সামুদ্রিক তাপের উপাদান কয়েক শতাব্দী বা এমনকি সহস্রাব্দ ধরে অব্যাহত থাকবে এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে আগামী প্রজন্মের ওপর। একই সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে হিমবাহগুলো দ্রুত গলছে। ২০২৩ সালে হিমবাহ আরও দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। ৭০ বছর আগে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে যেকোনো সময়ের তুলনায় বরফ গলার পরিমাণ বেশি। যা মৃত সাগরে ধারণ করা পানির পরিমাণের পাঁচ গুণের সমান। দ্রুত হিমবাহ গলে যাওয়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যা ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
অর্থনীতি ও মানুষ
পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পরিণতি বিশ্ব জুড়ে অনুভূত হচ্ছে। ২০২৪ সালে চরম আবহাওয়া মানুষ ও অর্থনীতির ধ্বংসাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে উপকূলবর্তী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাপপ্রবাহ থেকে শুরু করে প্রবল বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, দাবানল এবং মারাত্মক খরার নতুন বাস্তবতা মোকাবিলায় লড়াই করছে। ডব্লিউএমওর প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, জলবায়ু বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তা, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা এবং মানব স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। কীভাবে এই তীব্র জলবায়ু বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে এবং বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, জলবায়ু বিপর্যয় স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে, বৈষম্যকে প্রসারিত করছে, টেকসই উন্নয়নের ক্ষতি করছে এবং শান্তির ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। দুর্বলরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ক্রমবর্ধমান এ সংকট মোকাবিলায় ডব্লিউএমও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং জলবায়ু অভিযোজন কৌশলের ওপর জরুরি পদক্ষেপ নিতে জোর দিয়েছে। সাওলো বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতার অতিরিক্ত বৃদ্ধি জলবায়ুর চরম প্রভাব এবং ঝুঁকি বাড়ায়। ভবিষ্যতের ক্ষতি কমানো র জন্য গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতায় বিনিয়োগের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।
গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা তীব্রভাবে বাড়ছে। অর্থাৎ, ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে এটি ক্রমশ বাড়ছে। এমনকি গত ত্রিশ বছর ধরে শীতকাল ও বর্ষাকালেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম পড়ছে। আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক বিবিসিকে জানান, আগে বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তাপপ্রবাহ দেখা যেত। কিন্তু গত বছর সেই তাপপ্রবাহ সেপ্টেম্বরে গিয়ে ঠেকেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার (ন্যাপ) দেওয়া তথ্যে, শীতকাল (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) ও বর্ষা পূর্ববর্তী (মার্চ থেকে মে) সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। কিন্তু বর্ষা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) ও বর্ষা পরবর্তী (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়ছে। এসব কারণে শীতকালে বেশি শুষ্ক এবং বর্ষাকালে বেশি ভেজা আবহাওয়া থাকছে। ২০০৪ সালে ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩৪১ মিলিমিটার, ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে একই সময়ে ৪০৮ মিলিমিটার, ২০০৯ সালে ঢাকায় ১২ ঘণ্টায় ৩৩৩ মিলিমিটার, ২০২০ সালে রংপুরে ২৪ ঘণ্টায় ৪৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এসব তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমে বাড়ছে। এর মধ্যে রংপুরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিগত ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ভবিষ্যতে উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে এবং পশ্চিমাঞ্চলে এই পরিমাণ কমতে থাকবে। কিন্তু ২০৫০ সালে সারা দেশে বৃষ্টিপাত বাড়বে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশে গত ৩০ বছর ধরে উপকূলবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ৩ দশমিক ৮ থেকে ৫ দশমিক ৮ মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি)-এর তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলের মানুষের ঘরবাড়ি ও জীবিকা বিপন্ন হওয়ার কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১২ থেকে ১৮ শতাংশ ডুবে যাওয়ারও আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে নগরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এর সঙ্গে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে তাপমাত্রার এমন বৈরী আচরণের জন্য অপরিকল্পিত নগরায়ণেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ঢাকায় বছরে অসহনীয় গরম দিনের সংখ্যা গত ছয় দশকে অন্তত তিনগুণ বেড়েছে। আর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এই গরম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে বলছে, গত ২৮ বছরে ঢাকা থেকে ২৪ বর্গকিলোমিটারের সমআয়তনের জলাধার ও ১০ বর্গকিলোমিটারের সমপরিমাণ সবুজ কমে গেছে। ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আদিল খান বলেন, এখন জেলা-উপজেলা পর্যায়েও পুকুর বা জলাধার ভরাট করে পরিকল্পনাহীন ভবন উঠে চলেছে। নগরগুলোর প্রতিটি ভবন পরিকল্পিত না হলে এবং এলাকাগুলোতে সবুজের ভারসাম্য আনা না হলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক মো. শাখাওয়াত হোসাইন ওই বলেন, শহরগুলোকে একটি মাস্টারপ্ল্যানের আওতায় এনে, গ্রিনারি বা সবুজায়ন নিশ্চিত করতে হবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। শহরগুলোর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। শহরের সুবিধাগুলোকে শহরের বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে জনসংখ্যায় ঘনত্ব কমাতে হবে। পাশাপাশি ভবনগুলোকে পরিবেশবান্ধব করতে হবে। ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ খান বলছেন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য কংক্রিটের পরিমাণ কমাতে হবে এবং বনায়ন করতে হবে। বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে সেটা হলো ধ্বংসাত্মক নগরায়ণ। ঢাকার এমন ওয়ার্ড আছে যেখানে ৯০ ভাগই কংক্রিট। গরম বেশি অনুভূত হয়, কারণ নগর এলাকায় গাছপালা, জলাধার ধ্বংস করা হয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত ওপেন স্পেস রাখতেই হবে।